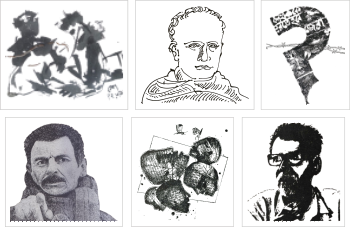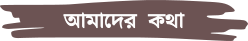সংস্কৃতি বিষয়ক যোগসূত্র বাংলাভাষায় প্রকাশিত সমাজচিন্তা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটি সাময়িক পত্র
সময়কাল: ১৯৯১-১৯৯৫
একটি ডিজিটাল সংরক্ষণ উদ্যোগ

আমাদের কথা
প্রায় তিন দশক আগে সংস্কৃতি বিষয়ক যোগসূত্র পত্রিকাটি বাংলা লিটল্ ম্যাগাজিনের সংবেদী পাঠকবর্গের কাছে এবং সারস্বত সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। যোগসূত্র নামেই ছিল তার পরিচিতি। বিনয় ঘোষের সম্পাদনায় উনিশ শো একানব্বই থেকে পঁচানব্বই, এই পাঁচ বছরে মোট এগারোটি সংখ্যার আত্মপ্রকাশের পরে একসময় যোগসূত্র বন্ধ হয়ে যায়। অনুরাগী পাঠকেরা দীর্ঘকাল পত্রিকার পুনঃপ্রকাশের অপেক্ষায় থেকেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যাশা আমরা মেটাতে পারিনি। নিজেদের সন্ধানী ঔৎসুক্য আমাদের প্রাণিত করেছিল কিছুকাল, আর তার খোরাক মেটাতে যতদিন পেরেছি, ততদিনই কাগজ চলেছে। অন্য কোনও দায় বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাড়িত করেনি। আমাদের কাজের দলটি ছোটো হলেও বাইরের একটা বড়ো অংশের সজাগ নজরের আওতায় আর আন্তরিক সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলাম আমরা। পত্রিকাকে ঘিরে সহৃদয় আগ্রহে উন্মুখ থাকতেন প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, উৎপলকুমার বসু, মিহির চক্রবর্তী, মাধব মিত্র, অনিরুদ্ধ লাহিড়ী আর বাঁধন দাসের মতো মানুষেরা। নানা সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও কবি বিনয় মজুমদার ক্রোড়পত্র এবং বিমূর্ততা বিষয়ক সংখ্যার সম্পাদনার কাজ সানন্দে করেছেন কবি উৎপলকুমার। মিহিরদা আমাদের এই সাম্প্রতিক উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। চিত্তপ্রসাদ সংখ্যার মূল ছবি সংগ্রহ ও মুদ্রণ প্রকরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন দেবাশিস দত্ত। পাঠককুলের কাছে এমন আরও কয়েকটি সংখ্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। গৌতম ভদ্র সম্পাদিত কথকতা বিষয়ক সংখ্যাটিতো বর্তমান প্রজন্মের গবেষকদেরও জরুরি বলে মনে হতে পারে। মুদ্রণের খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের চাহিদার শেষ ছিল না। সবটুকু সহ্য করেছেন ছাপাখানা ইম্প্রিন্টার মালিক শোভনলাল কুমার। শিক্ষিত, সজ্জন এই মানুষটি কীভাবে যেন আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমাদের সকলের প্রিয় কৃষ্ণাদি (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রুফ দেখে দিয়েছেন কিছু দিন। ছিলেন অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা, যাঁরা নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন জুগিয়ে পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, অর্থাভাবে আমাদের কাগজ বন্ধ করতে হয়নি।
এতকাল অতিক্রান্ত হলেও অনেকেই পত্রিকার কোনও কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করতে চেয়ে আমাদের অনুরোধ করেন। মুদ্রিত সংখ্যার বিকল্প হিসেবে সবকটি সংখ্যাই উৎসাহী জনের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই আয়োজন। নিজেদের সংরক্ষিত সংগ্রহের ঝুলি ঝেড়ে এগারোটি প্রকাশিত সংখ্যাই জড়ো করা সম্ভব হয়েছে আর তার সবটাই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া গেল। এমনটাও ভাবা হয়েছিল যে মুদ্রিত লেখাগুলোকে পাঠের সুবিধার্থে নতুন করে টাইপ করা হবে কিনা। তাতে অবশ্য তিন দশক আগের মুদ্রণরীতি, লেটারপ্রেসে ছাপার বিশেষত্ব, টাইপ নির্বাচন, লে আউট ও অলংকরণ ভাবনা তার কিছুই ধরা পড়ত না। সবকিছুই তো সময়ের চিহ্ন বহন করছে। দলিল বা ইতিহাস যাই ভাবা হোক, তার টান এড়ানো গেল না।
ঐতিহ্য অনুসারী হয়েও চেনা আঙিনার বাইরে নতুনতর পরিসর খোঁজার একটা প্রবণতাই হয়তো যোগসূত্রকে কিছুটা বিশেষতা দিয়েছিল। আর এই দলছুট ভাবনার অন্যতম দিশারী ছিল যে মানুষটি, সেই রাঘবদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) তো কবেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ও থাকলে সন্দেহাতীতভাবে আজকের এই উদ্যোগেও ঝিলিকের মতো ব্যতিক্রমী কোনও মাত্রা যোগ হত। অসুস্থ বিনয়দাকেও এবার শরিক করতে পারলাম না। অথচ ওর চিন্তা, উদ্যম আর প্রাণশক্তি আমাদের চিরদিন বিস্মিত করেছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কল্যাণদা (ভট্টাচার্য) নেপথ্যে থেকে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। একই ভাবে সঙ্গে আছেন বিশাখাদি (বন্দ্যোপাধ্যায়)।
পত্রিকা করতে এসে বহু মানুষের সান্নিধ্য লাভ আমাদের কাছে বাড়তি এক প্রাপ্তি। সোমনাথ হোর, বারীন সাহা, নির্মল গুহ রায়, খালেদ চৌধুরী, রাজ্যেশ্বর মিত্র এবং বিনয় মজুমদার, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের অভিজ্ঞতা, কোথাও বা একটু নৈকট্য, সেসব ভোলার নয়। পারস্পরিকতা, সহযোগিতা, শিক্ষা আর বিনিময়ের একটা পরিসর গড়ে তোলা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই স্মৃতি আজও আনন্দের সঞ্চার করে। বাংলাভাষা চর্চার একটি সিরিয়াস প্রয়াস হিসেবে যোগসূত্র প্রকাশনাকে আমরা সামাজিক আন্দোলন বলেই মনে করেছিলাম সেদিন। আজকের এই উদ্যোগ তারই জের হিসেবে বহাল থাকুক, এইটুকুই চাই।
পাঠক, আমাদের নমস্কার নেবেন।
১লা বৈশাখ, ১৪৩২